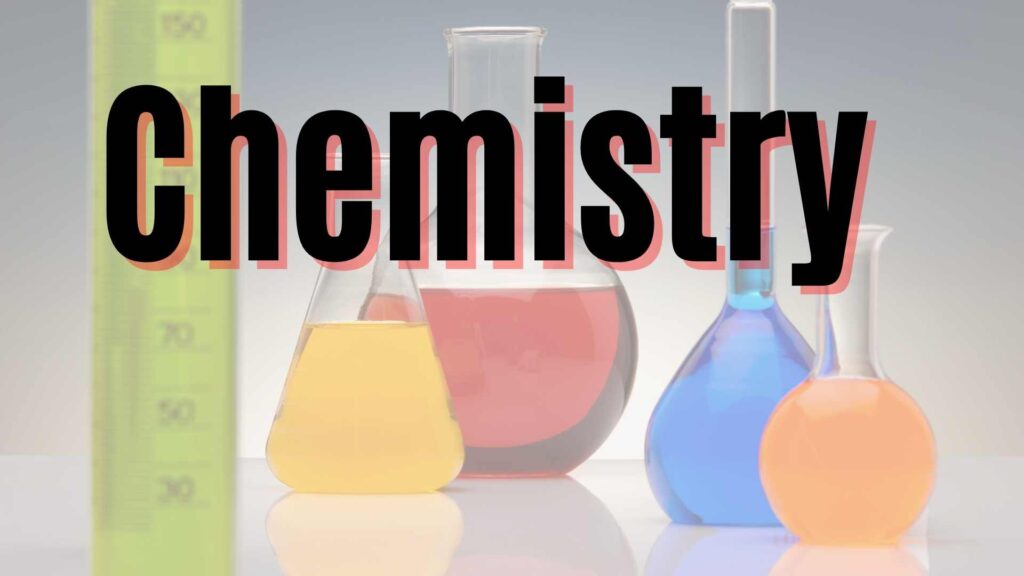নবম দশম/এসএসসি রসায়ন একাদশ অধ্যায় খনিজ সম্পদ-জীবাশ্ম এর পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি,জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর নিচে দেওয়া হলো। এসএসসি রসায়ন ১১ অধ্যায় খনিজ সম্পদ-জীবাশ্ম একাদশ অধ্যায় খনিজ সম্পদ-জীবাশ্ম পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ⇒ জীবাশ্ম জ্বালানি : শক্তির অতি পরিচিত উৎস হলো কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। কোটি কোটি বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে বিশাল বিশাল বনভ‚মি ছিল। বনভ‚মিতে যেসব গাছপালা, জীবজন্তু ছিল প্রচণ্ড ভ‚মিকম্প বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বা অন্য কোনো কারণে মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে জমতে থাকে। এদেরই দেহাবশেষ জীবাশ্ম। ভ‚অভ্যন্তরভাগে প্রচণ্ড চাপে ও তাপে বায়ুর অনুপস্থিতিতে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এদের ধ্বংসাবশেষ ক্রমশ কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়। এ জীবাশ্ম কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে খনি থেকে তুলে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। তাই এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। ⇒ পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল : শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল। খনি থেকে যে তেল আহরিত হয় তা অপরিশোধিত তেল যা মূলত হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য কিছু জৈব যৌগের মিশ্রণ। অপরিশোধিত তেলকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য এর বিভিন্ন অংশকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। পেট্রোলিয়ামে বিদ্যমান উপাদানের স্ফুটনাংকের ওপর ভিত্তি করে তেল পরিশোধনাগারে পৃথকীকৃত বিভিন্ন অংশের নাম পর্যায়ক্রমে পেট্রোলিয়াম গ্যাস, পেট্রোল (গ্যাসোলিন), ন্যাপথা, কেরোসিন, ডিজেল তেল, লুব্রিকেটিং তেল ও বিটুমিন। পেট্রোলের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্বালানি ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। ⇒ প্রাকৃতিক গ্যাস : খনিতে পেট্রোলিয়াম যে প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক গ্যাসের সৃষ্টির প্রক্রিয়াও একই রকম। সাধারণত খনির উপরের অংশে গ্যাস আর নিচের দিকে খনিজ তেল থাকে। খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উভয়ই জৈব পদার্থ। এগুলো কার্বন ও হাইড্রোজেনের বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণের ফলে গঠিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (8০%)। এছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকে ইথেন (7%), প্রোপেন (6%), বিউটেন ও আইসো বিউটেন (4%), পেনটেন (3%)। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের হার 99.99%। প্রাকৃতিক গ্যাসকে বায়ুতে পোড়ালে তাপশক্তি পাওয়া যায়। ⇒ হাইড্রোকার্বন : কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত যৌগসমূহকে হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন : CH4, C2H6, C6H6, C6H12 প্রভৃতি। আণবিক গঠন অনুযায়ী হাইড্রোকার্বন প্রধানত দুই প্রকার। যথা : অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন ও অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। মুক্ত শিকল ও বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন। মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনসমূহ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যেসব হাইড্রোকার্বনে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন থাকে তাদের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন : ইথেন, প্রোপেন। যেসব হাইড্রোকার্বনে কার্বন-কার্বন পরমাণুর মধ্যে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন বা একটি ত্রিবন্ধন থাকে তাদের অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন : ইথিন, ইথাইন ইত্যাদি। ⇒ অ্যালকেন : সকল সম্পৃক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন বলা হয়। এদের সাধারণ আণবিক সংকেত CnH2n+2 (n = 1, 2, 3 ………)। এ শ্রেণির প্রথম (n = 1) সদস্যের নাম মিথেন CH4 এবং দ্বিতীয় সদস্য (n = 2) হচ্ছে ইথেন C2H6। প্রতিটি অ্যালকেনের নামের শেষে এন (ane) থাকবে। অ্যালকেনের C – C এবং C – H বন্ধনসমূহ শক্তিশালী হওয়ায় এরা রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এরা সাধারণ অবস্থায় তীব্র এসিড, ক্ষারক ও জারক বা বিজারক পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। এজন্য এদের ‘প্যারাফিন’ বা আসক্তিহীন বলা হয়। তবে বায়ু বা অক্সিজেন এবং ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে। ⇒ অ্যালকিন : যেসব অসম্পৃক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কমপক্ষে দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে দ্বিবন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের অ্যালকিন বলে। এদের সাধারণ আণবিক সংকেত CnH2n। এ শ্রেণির প্রথম সদস্যের নাম ইথিলিন (C2H4)। প্রতিটি অ্যালকিনের নামের শেষে ইন (ene) থাকবে। অ্যালকিনসমূহের রাসায়নিক ধর্ম কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ দ্বিবন্ধনের কারণে এরা অনেক সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তখন এ দ্বিবন্ধন ভেঙে যায় এবং একক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। ⇒ অ্যালকাইন : যেসব অসম্পৃক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কমপক্ষে দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে ত্রিবন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের অ্যালকাইন বলে। এদের সাধারণ আণবিক সংকেত CnH2n-2। এ শ্রেণির প্রথম সদস্যের নাম অ্যাসিটিলিন (CH – CH)। মূল হাইড্রোকার্বনের নামের শেষে এন (ane) বাদ দিয়ে সেখানে আইন (-yne) যোগ করলে অ্যালকাইনের নাম পাওয়া যায়। ⇒ অ্যালকোহল : সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অণু থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রক্সিল (- OH) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে যৌগসমূহ গঠিত হয়, তাদের অ্যালকোহল বলা হয়। অ্যালকেন থেকে উদ্ভূত অ্যালকোহলসমূহের সাধারণ সংকেত CnH2n+1OH। এ শ্রেণির প্রথম সদস্য হচ্ছে মিথানল বা মিথাইল অ্যালকোহল CH3OH, দ্বিতীয় সদস্য হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল CH3CH2OH। অ্যালকোহলের বিক্রিয়া প্রধানত -OH গ্রুপের বিক্রিয়া। ⇒ অ্যালডিহাইড : সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অণু থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু -CHO গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে যৌগসমূহ গঠিত হয়, তাদের অ্যালডিহাইড বলা হয়। অ্যালকেন থেকে উদ্ভূত অ্যালডিহাইডের সাধারণ সংকেত CnH2n+1, CHO। এ শ্রেণির প্রথম সদস্য হচ্ছে ফরম্যালডিহাইড (HCHO)। ⇒ জৈব এসিড : একটি কার্বক্সিলমূলক বিশিষ্ট অ্যালিফেটিক জৈব যৌগসমূহকে জৈব এসিড বা ফ্যাটি এসিড বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত RCOOH। প্রথম ফ্যাটি এসিডের নাম মিথানয়িক এসিড (HCOOH)। দ্বিতীয় ফ্যাটি এসিডের নাম ইথানয়িক এসিড (CH3COOH)। ফ্যাটি এসিডসমূহের কার্যকরী মূলক হচ্ছে -COOH। প্রায় সব বিক্রিয়ায় এ মূলক অংশগ্রহণ করে। ⇒ পলিমার : একই পদার্থের অসংখ্য অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে বৃহৎ অণু গঠন করে তাকে পলিমার বলে। মেলামাইনের থালা-বাসন, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, কার্পেট, পিভিসি পাইপ, পলিথিনের ব্যাগ, সিল্কের বা উলের কাপড়, নাইলনের সুতা, রাবার সবই পলিমার। দুই ধরনের পলিমার আছে- প্রাকৃতিক পলিমার ও কৃত্রিম পলিমার। ⇒ প্রাকৃতিক পলিমার : প্রাকৃতিকভাবে অনেক পলিমার উৎপন্ন হয়। যেমন : উদ্ভিদের সেলুলোজ ও স্টার্চ দুটোই পলিমার যা বহুসংখ্যক গøুকোজ অণুযুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। প্রোটিন অ্যামাইনো এসিডের পলিমার। ইনসুলিন নামক পলিমারে দুটি অ্যামাইনো এসিড থাকে। রাবার নামক গাছের কষ একটি প্রাকৃতিক পলিমার। ⇒ কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক : সকল প্লাস্টিক দ্রব্য কৃত্রিম পলিমার। প্লাস্টিক শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ চষধংঃরশড়ং থেকে যার অর্থ গলানো সম্ভব। যেসব প্লাস্টিক গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে যে কোনো আকার দেওয়া যায়, সেগুলো কৃত্রিম পলিমার। রাসায়নিক পদার্থ বিশেষত দ্বিবন্ধন বিশিষ্ট অ্যালকিন, অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল, অ্যামিন, জৈব এসিডের পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্লাস্টিক প্রস্তুত করা হয়। ⇒ পলিমারকরণ : উচ্চতাপ (2০০0C) ও উচ্চচাপে (1০০০ বায়ুচাপে) অসংখ্য অ্যালকিন অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আকৃতির অণু গঠন করে। এ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বৃহৎ অণুকে পলিমার এবং বিক্রিয়াকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। যে অসংখ্য বিক্রিয়ক অণু যুক্ত হয় তাদের প্রত্যেকটি অণুকে মনোমার বলে। ⇒ জৈব ও অজৈব যৌগের পার্থক্য : কার্বন ও হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগসমূহকে জৈব যৌগ বলে। অর্থাৎ সকল হাইড্রোকার্বনই জৈব যৌগ। জৈব যৌগসমূহ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে এবং অজৈব যৌগসমূহ আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। কিছু সমযোজী যৌগ থাকে যারা আয়নিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং কিছু আয়নিক যৌগ থাকে যারা সমযোজী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। নবম দশম শ্রেণির রসায়ন ১১তম অধ্যায় জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর প্রশ্ন \ 1 \ রিফাইনিং কী? উত্তর :