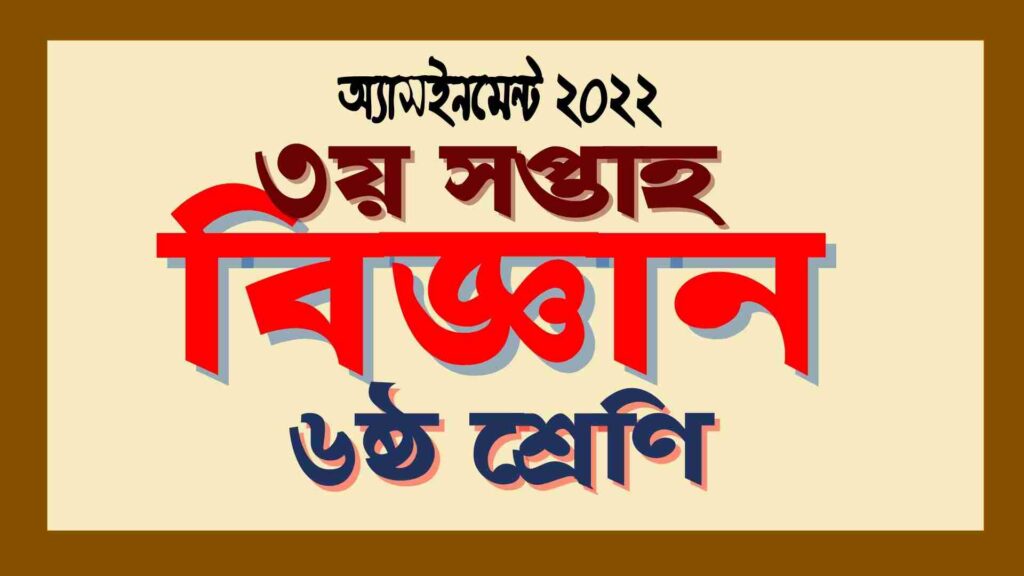এসএসসি সাধারণ বিজ্ঞান নবম অধ্যায় দুর্যোগের সাথে বসবাস পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যে লক্ষণীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। যেমনÑ ১. ঋতুর পরিবর্তন : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুচক্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে দেখা যাচ্ছে। শীতকাল সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে কমে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ছে এবং তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে ৪৫Ñ৪৮ সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠছে। ২. বন্যা : জলবায়ুুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন ও অসময়ে প্রলয়ংকরী বন্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চল বন্যা প্রবণ নয়, যেমন যশোর, ঢাকা সে সকল অঞ্চলও এখন বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। ৩. নদীভাঙন : সা¤প্রতিককালে নদীভাঙন অনেক বেড়ে গেছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিগত তিন দশকে প্রায় ১,৮০,০০০ হেক্টর জমি শুধু পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিন নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। ৪. খরা : জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টিপাতের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলছে। এ কারণে বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ৫. পানির লবণাক্ততা : জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মূল ভ‚খণ্ডে ঢুকে নদনদী ও ভ‚গর্ভস্থ পানি ও আবাদি জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। ৬. সামুদ্রিক প্রবাল ঝুঁকি : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক প্রবালের জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। ১৯৬০ সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে পরিমাণ প্রবাল ছিল, ২০১০ সালে তার প্রায় ৭০% বিলীন হয়ে গেছে। ৭. বনাঞ্চল : লবণাক্ত পানির প্রভাব, সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বনাঞ্চল দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। ৮. মৎস্য সম্পদ : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রহ এবং জৈবিক নানা প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। ৯. স্বাস্থ্যঝুঁকি : জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রলয়ংকরী বন্যায় পানিদূষণ ও পানিবাহিত রোগ, বিশেষ করে কলেরা, ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। ১০. জীববৈচিত্র্য : জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০% জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়ছে। ১১. সাইক্লোন : সাইক্লোনের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করছে। পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির কারণ : বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি স্থান এখন নানারকম পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে করে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১০ বিলিয়ন। এর কারণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সব রকমের চাহিদা বেড়ে যাবে ও কর্মসংস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি হবে। পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সমস্যা হলো নগরায়ন। এটিও মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির জন্য বর্তমান সময়ে দায়ী করা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতাকে। এর মূল কারণ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ ওজোন, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প এই গ্যাসগুলোর বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাওয়া। এর ফলে প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালার দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডের শোষণ কমে যাচ্ছে। যার ফলে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বনশূন্য করা আরেকটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। এর জন্যও দায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয় : মানুষের অবিবেচনাসুলভ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্যোগ সৃষ্টি করছে। এসব দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি দুর্যোগের বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলোÑ ১. বন্যা : নদনদী ভরাট হয়ে যাওয়া, ভারী বর্ষণ বা উজানে অববাহিকা থেকে পানি আসা, মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রায় প্রতিবছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা প্রলয়ংকরী আকার ধারণ করছে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে নদনদী খনন করে এদের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। দরকারি স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিতে হবে। এছাড়া নদীর পাড়ে গাছ লাগানো, পানি প্রবাহের জন্য ¯øুইস গেট নির্মাণ ইত্যাদিও বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার কৌশল হতে পারে। ২. খরা : খরার জন্য দায়ী কারণগুলো হলো বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়া, ভ‚গর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ উত্তোলন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজান থেকে পানি প্রত্যাহার, পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয় ইত্যাদি। খরা মোকাবিলার জন্য করণীয় হলোÑ জলাশয়ের পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা; মাটিতে পানি কম থাকলেও জন্মাতে পারে যেমনÑ গম, পিঁয়াজ, কাউন ইত্যাদি চাষ করা। চাষাবাদে অনেক বেশি পানি লাগে এমন ফসল চাষে নিরুৎসাহিত করা যেমনÑ ইরি ধান; বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করা ইত্যাদি। ৩. সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় : সাইক্লোন সৃষ্টির মূল কারণ হলো নিম্নচাপ ও উচ্চতাপমাত্রার প্রভাব। দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায় ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করে; উপক‚লীয় এলাকায় বাঁধ তৈরি করে; মজবুত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও প্রচুর গাছপালা রোপণ করে। ৪. সুনামি : সমুদ্র তলদেশে ভ‚মিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভ‚মিধস এবং নভোজাগতিক ঘটনা সুনামি সৃষ্টির কারণ। পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানোর মাধ্যমে সুনামি মোকাবিলা করা যায়। ৫. এসিড বৃষ্টি : এসিড বৃষ্টি সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ জড়িত। প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, বজ্রপাত, গাছপালার পচন ইত্যাদি। মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসসমূহের নিঃসরণ। কয়লা পরিশোধন দ্বারা ও বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার করে এসিড বৃষ্টি মোকাবিলা করা যায়। ৬. টর্নেডো বা কালবৈশাখী : টর্নেডো বা কালবৈশাখীর জন্য লঘু বা নিম্নচাপ সৃষ্টি প্রধান কারণ। দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্বাসন কাজ করাই হলো এ দুর্যোগের সমাধান। ৭. ভ‚মিকম্প : ভ‚গর্ভের টেকটনিক প্লেট এর স্থান পরিবর্তনের ফলেই ভ‚মিকম্প সৃষ্টি হয়। ভ‚মিকম্প সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মাণ করে এবং পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার দ্বারা ভ‚মিকম্প মোকাবিলা করা যায়। সুস্থ জীবনযাপনে মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব : বিশুদ্ধ বাতাস ও নিরাপদ পানি আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। নির্মল বাতাস ও সুপেয় পানির অভাবে জীবজগৎ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বাতাস ও পানির মতো পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই আমাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক। এই পরিবেশ যদি মানসম্মত ও উন্নত না হয় তা সকল জীব বৈচিত্র্যের জন্য বড় রকমের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে ও আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে পাশাপাশি জনগণকেও সচেতন করে তুলতে হবে। প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য : প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা হলো আমাদের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ হলো পানি, বাতাস, মাটি, খনিজ সম্পদ, গাছপালা, প্রাণিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রতিটি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভ‚মিকা না নিই, গাছপালা বনজ সম্পদ নিধন বন্ধ না করি, বাতাস, পানি ইত্যাদির দূষণ বন্ধ না করি, তাহলে আমাদের এই প্রকৃতি আর বাসযোগ্য থাকবে না এবং আমাদের কোনো অস্তিত্বও থাকবে না। প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল : প্রকৃতি সংক্ষণশীলতার বেশ কয়েকটি কৌশল আছে। এগুলো হলোÑ১. সম্পদের ব্যবহার কমানো, ২. দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা, ৩ একই জিনিস সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করা, ৪. ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করা, ৫. প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরি রক্ষা করা। অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ১. কোন দুর্যোগটি শুধুমাত্র সাগরে সংঘটিত হয়? ক কালবৈশাখী খ ভ‚মিকম্প সুনামি ঘ বন্যা ২. গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণÑ র. যানবাহন